এই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গেই সমাপ্ত হল ‘রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ’ গ্রন্থমালা। রয়েল সাইজের চার খণ্ডে মোট ২৩৬৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দুই দশকের কর্মজীবনের বিস্তৃত বিবরণ। যেসব প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেখানে টীকা দেওয়া হয়েছে প্রায় ১৪০০টি। এ ছাড়া সংযোজিত হয়েছে ‘রবীন্দ্র কালপঞ্জি’ এবং ‘ব্যক্তি পরিচিতি’। চিত্র প্রতিলিপি পাওয়া যাবে ৪৮টি। চতুর্থ খণ্ডে বিশেষরূপে সঙ্কলিত ‘রবীন্দ্র কালপঞ্জি’ এবং ‘নির্বাচিত ব্যক্তি পরিচিতি’ অধ্যায় এই গ্রন্থমালাকে নিছক সংবাদ কর্তিকার সঙ্কলন থেকে উন্নীত করে মর্যাদা দিয়েছে কোষগ্রন্থের। রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় ‘রবীন্দ্র প্রসঙ্গ’ হবে আমাদের নিত্যসঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘…আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংলাদেশে এসেছি। আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক। এখানেই থেমে গেছে। তারপর যে আমার আর কোন সাধনায় দেশ আমাকে আহ্বান করেছে সে খবর পৌছতে বিলম্ব হল…’। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ’ গ্রন্থে কবির সেই স্বল্পজ্ঞাত অন্য পরিচয় পাঠকদের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়; কিন্তু কবির কর্মজীবন সম্বন্ধে এমন বিস্তৃত বিবরণ অন্য কোথাও সুলভ নয়। কবির সাহিত্যকে সম্যক উপলব্ধির জন্য তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে পরিচয় থাকা আবশ্যক। কারণ, কবি নিজেই বলেছেন—’আমার বাক্যের রচনা আর কর্মের রচনা একই পথে চলে’। চতুর্থ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক সংবাদ কর্তিকাগুলি বিন্যস্ত করা হয়েছে তিনটি অধ্যায়ে; যথা—‘ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব’, ‘মহাপ্রয়াণ’ এবং ‘স্মরণ’। প্রথম অধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে কবিকে ভূষিত করা। এর পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কখনও ব্রিটেনের বাইরে গিয়ে কাউকে সম্মান জানায়নি। আর একটি বিশেষ কারণে এই সংবর্ধনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯২ সালে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু যখন কবিকে সাম্মানিক উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তখন চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন প্রস্তাবটি নাকচ করে মন্তব্য করেছিলেন—‘there were more distinguished men in India than Tagore.’ অন্তিম শয্যায় রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করে কবি কেমন করে কাব্যসৃষ্টি করেছেন তার অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ‘মহাপ্রয়াণ’ অধ্যায়ে। মৃত্যুর পর দেশবিদেশ থেকে আসতে লাগল স্মৃতিরক্ষার বিচিত্র সব প্রস্তাব। প্রস্তাব করতে আমরা কল্পতরু, রক্ষা করতে চরম অনীহা। তাই বানার্ড শ’, এইচ. জি. ওয়েলস, আলডুস হাক্সলি প্রমুখ মনীষীদের এবং দেশের নাগরিকদের প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপ পায়নি। শুধু বিশ্বভারতীর কাঠামো রক্ষা পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়, এবং প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রবীন্দ্র নামাঙ্কিত একটি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন। সেদিনকার সাহিত্যিকেরা পুরস্কারের অর্থমূল্য হাজার টাকার বেশি ভাবতেও পারেননি। ‘স্মরণ’ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে শোকসভা ও স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনার বিবরণ। বর্তমান খণ্ডে দুটি বিশেষভাবে সঙ্কলিত অধ্যায় এই গ্রন্থমালার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। একটি হল ‘রবীন্দ্র কালপঞ্জি’,—দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে আছে ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিজন’। এখানে কবির জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যাবে, আর পাওয়া যাবে তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিবরণ। দ্বিতীয় অংশটি হল ‘দেশ ও বিদেশ’। কবির বিশ্বসচেতনতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবগত আছি। দেশ বা বিদেশের বড় বড় ঘটনার ঢেউ তাঁর মনে অভিঘাতের সৃষ্টি করত এবং ছড়িয়ে পড়ত তাঁর কর্মে ও সাহিত্যে। এখানে তাই সংক্ষেপে সঙ্কলিত হয়েছে বিশ্বের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার দিকচিহ্নগুলি। পাওয়া যাবে এই কালখণ্ডে প্রকাশিত বইয়ের বিবরণ, সামাজিক ঘটনাবলীর কথা, নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নাম ইত্যাদি। বিশ্বভাবনার প্রবাহে কবির অবস্থিতি কোথায়, তা-ও এই ঘটনাপঞ্জি থেকে উপলব্ধি করা যাবে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল ‘নির্বাচিত ব্যক্তি পরিচিতি’। বিশেষ করে শেষ দুই দশকে কবি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন বা যাঁদের নাম রচনা ও ভাষণে উল্লেখ করেছেন তেমন প্রায় ৬৫০ জনের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এখানে ও টীকায়।
[Source: Ananda Publishers]



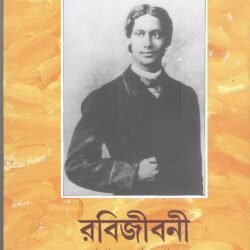
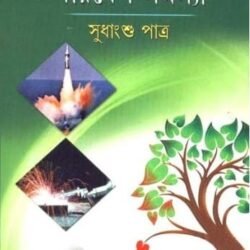
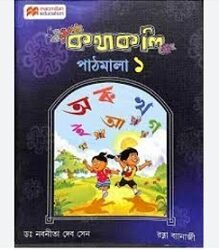
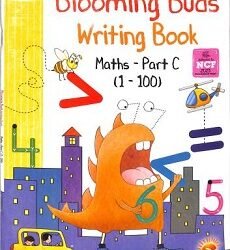
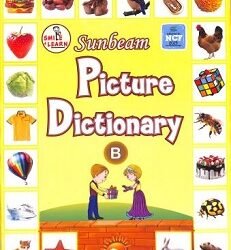
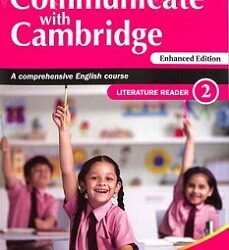
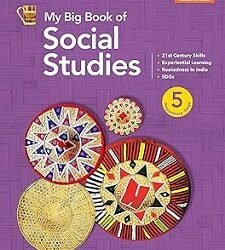

Reviews
There are no reviews yet.